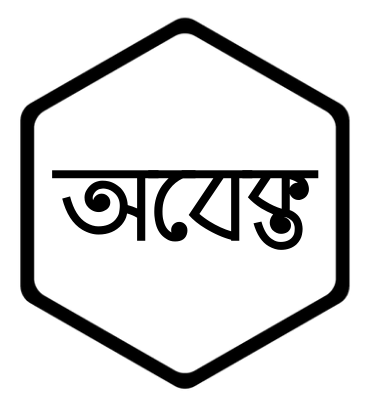This is an old revision of the document!
নাগার্জুন
নাগার্জুন বৌদ্ধ কালচারের সবচেয়ে বড় দার্শনিক। তার যুগ ঠিক করার সবচেয়ে ভালো উপায় ‘রত্নাবলী’ যা তিনি সম্ভবত ১৭০ থেকে ২২০ সালের মধ্যে বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের অমরাবতীতে বসে লিখেছিলেন। একশর বেশি বই তার লেখা বলে দাবী করা হয়, তবে ওয়েস্টারহফ নাগার্জুনের উপর বই লিখেছেন ছয়টির উপর ভিত্তি করে: মূলমধ্যমককারিকা, যুক্তিষষ্ঠিকা, শূন্যতাসপ্ততি, বিগ্রহব্যাবর্তনী, বৈদল্যপ্রকরণ ও রত্নাবলী। যুক্তিসমগ্র নামে পরিচিত এই বইগুলো পদ্যে লেখা, তবে সাথে গদ্য ভাষ্য আছে। গত দুই হাজার বছরে ভারত চীন ও তিব্বতের অনেক লেখক যুক্তিসমগ্রের বিভিন্ন বইয়ের উপর ছোট বড় অনেক ভাষ্য লিখেছেন।
নাগার্জুনের দর্শনের নাম ‘মধ্যমক’ যার ভিত্তি শূন্যতা। এখানে শূন্যতা পুরাপুরি ঋণাত্মক শব্দ, মানে শূন্যতা নিজে কোনো জিনিস না, কেবল কোনো জিনিসের অনুপস্থিতি বা অনস্তিত্ব। মধ্যমকে প্রধানত যে শূন্যতা নিয়ে কথা বলা হয় তা হলো স্বভাবের শূন্যতা, অর্থাৎ স্বভাবহীনতা। কোনকিছুরই স্বভাব নাই, সবকিছুই স্বভাবশূন্য। শূন্যতা আলাদা করে বুঝার কিছু নাই, স্বভাব বুঝলেই সাথে সাথে স্বভাবশূন্যতা বুঝা যাবে। স্বভাব দুই ধরনের হতে পারে: অব্জেক্টিভ ও সাব্জেক্টিভ। কোনকিছুর অন্তর্নিহিত এসেন্স ও সাবস্টেন্স হচ্ছে তার অব্জেক্টিভ স্বভাব। আর তাকে ভাবামাত্র আমাদের মন তার উপর যে স্বভাব আরোপ করে তা হলো সাব্জেক্টিভ স্বভাব। অব্জেক্টিভ স্বভাব যুক্তির মাধ্যমে ভুল প্রমাণ করা যায়, কিন্তু সাব্জেক্টিভ স্বভাব যুক্তি দিয়ে দূর করা সম্ভব না, সম্ভব কেবল নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে। যেমন, ত্রিমাত্রায় বাস করেও আমরা গণিতের মাধ্যমে খুব সহজে একটা চতুর্মাত্রিক ব্লকের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারি, কিন্তু ম্যাথের আগল থেকে তাকে মনের নাগালে আনা খুব কঠিন, এর জন্য অনেক চর্চার দরকার। দ্বিমাত্রায় বাস করা কেউ যেভাবে অনেক কষ্টে ত্রিমাত্রিক কিউবের ছায়া ধরার চেষ্টা করে সেভাবেই অনেক চর্চার মাধ্যমে আমরা হয়ত ত্রিমাত্রায় বসে চতুর্মাত্রিক ব্লক কল্পনার চেষ্টা করতে পারি। মধ্যমক এই কারণে একইসাথে যুক্তি ও চর্চার উপর গুরুত্ব দেয়।
স্বভাবের শূন্যতা প্রমাণ করতে হলে নেগেশনকে নৈয়ায়িকদের মতো করে ভাবলে হবে না। ন্যায় দর্শনের লোকেরা মনে করত, শুধু মূর্ত জিনিসই নেগেট করা যায়, বিমূর্থ জিনিস নেগেট করার কিছু নাই। যেমন, ‘এখানে একটা বাটি আছে’ বলার অর্থই ‘এই খানে’ আছে বলা; স্বয়ং বাটিকে নেগেট করার কিছু নাই কারণ তা বিমূর্ত ধারণা, বাটিটা এই খানে আছে না অন্য খানে আছে সেটাই শুধু নেগেশন বা এফার্মেশনের বিষয়। নাগার্জুন কোনকিছুর স্বভাব নেগেট করার জন্য ‘চতুষ্কোটি’ নামে এক যুক্তি ইউজ করেন; এরকম নাম কারণ এর মাধ্যমে একটা কথা নিয়ে চার ধরনের পজিশন বাতিল করা হয়: কথাটা, তার নেগেশন, দুইটা একসাথে এবং কোনোটাই না। এই যুক্তি খাটানোর সময় খেয়াল রাখতে হয় যে কোনো কোনো নেগেশন তার অব্জেক্টের বৈশিষ্ট্য সরাসরি ধরিয়ে দেয়, কোনো কোনোটা দেয় না। যেমন, ‘আপেলটা লাল না’ বলার অর্থই তা অন্য কোনো রঙের, কিন্তু ‘গ্র্যাভিটি লাল না’ বলার অর্থ এই না যে তা অন্য কোনো রঙের।
যেকোনো জিনিস বা ঘটনার ভিতরে ঢুকে দেখানো যায় যে তার স্বভাব নাই। কিন্তু নাগার্জুন তিনটা জিনিসের স্বভাবশূন্যতা নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত: কার্যকারণ, গতি ও আত্ম। কার্যের সাথে কারণের সম্পর্ক নেচারের দিক দিয়ে হতে পারে বা সময়ের দিক দিয়ে হতে পারে। কার্য ও কারণ হয় একই, নয় আলাদা, নয় তারা একে অপরের অংশ। আবার কার্য কারণের আগে, পরে বা একই সময়ের হতে পারে। নাগার্জুন এই সব ধারণাই বাতিল করেন এবং এর মাধ্যমে বুঝাতে চান কার্যকারণ মনের বাইরে থাকা কোনো অব্জেক্টিভ জিনিস না। জগতে কোনো অব্জেক্টিভ কার্য নাই, কারণ নাই এবং দুয়ের মধ্যে কোনো পরম কার্যকারণ সম্পর্কও নাই, তিনটাই মনের উপর নির্ভর করে। গতির স্বভাবশূন্যতা মধ্যমকের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়াটা যেমন গতি তেমনি এক জীবন থেকে আরেক জীবনে যাওয়াও এক ধরনের গতি। চলন ও চালক বলে যেমন আলাদা কিছু নাই, দ্রব্য (একটা বস্তু) ও গুণ (তার বৈশিষ্ট্য) বলেও আলাদা কিছু নাই। বস্তু ও বৈশিষ্ট্য অব্জেক্টিভলি বাস্তব না বরং মানুষের ভাষা ও ভাব দিয়ে বানানো ধারণা। বৈশিষ্ট্য থাকলেই বস্তু থাকতে হবে না। আত্মের গুণ থাকলেও আত্ম কোনো সাবস্টেন্স না, আত্ম একটি প্রসেস। প্রসেস-আত্মকে সাবস্টেন্স-আত্ম ভেবে ভুল করাই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধান শুধু যুক্তি দিয়ে সম্ভব না, দ্বিমাত্রিকের তিন মাত্রা দেখার মতোই প্রয়োজন চর্চা।
নাগার্জুনের জ্ঞানতত্ত্বও শূন্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য আত্মের কোনো অন্তর্নিহিত অব্জেক্টিভ উপায় নাই, একেক ক্ষেত্রে একেক সাব্জেক্টের কাছে একেক উপায় থাকতে পারে। জ্ঞানার্জনের উপায় নির্ভর করে কন্টেক্সটের উপর। উপায় নিজেও স্বভাবশূন্য, কিন্তু উপায়ের অস্তিত্ব পুরাপুরি অস্বীকার করলে শূন্যতা জানাও অসম্ভব হতো, এজন্যই দরকার প্রেক্ষাপট। ভাষা নিয়ে মাধ্যমিকদের মূল কথা হলো, নাগার্জুনের কোনো থিসিস বা পজিশন নাই। অর্থাৎ তার এমন কোনো থিসিস নাই যা নির্দিষ্ট কোনো সিমেন্টিক্স দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে। কারণ বিশ্ব ও ভাষার মধ্যে কোনো অব্জেক্টিভ সম্পর্ক নাই। এমন কোনো অব্জেক্টিভ বিশ্ব নাই যার বিভিন্ন বস্তুকে ভাষার বিভিন্ন শব্দ দিয়ে সত্যিকার অর্থে ধারণ করা যায়। ভাষা যেমন মনের নির্মাণ, বিশ্বও তেমনি মনের অধীন।
রেফারেন্স
- ইয়ান ওয়েস্টারহফ, ‘নাগার্জুনা’স মাধিয়ামাকা: এ ফিলোসফিকেল ইন্ট্রোডাকশন,’ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৯।