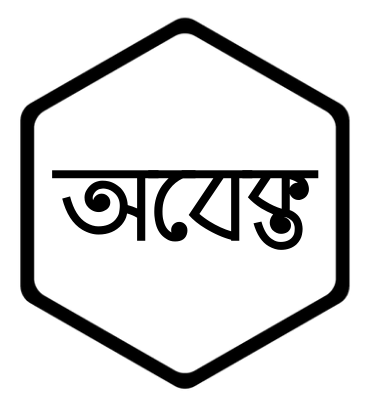Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| bn:un:almagest-revolutions [2025/03/01 01:03] – asad | bn:un:almagest-revolutions [2025/03/02 02:27] (current) – asad | ||
|---|---|---|---|
| Line 14: | Line 14: | ||
| ===== - এরিথমেটিক থেকে জিওমেট্রি ===== | ===== - এরিথমেটিক থেকে জিওমেট্রি ===== | ||
| - | ব্যাবিলনিয়া' | + | ব্যাবিলনিয়া' |
| পিথাগোরাসের অনুসারীরা প্রথম ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল যে পৃথিবী একটা গোলক (স্ফিয়ার), | পিথাগোরাসের অনুসারীরা প্রথম ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল যে পৃথিবী একটা গোলক (স্ফিয়ার), | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
| ===== - জিওমেট্রি থেকে ফিজিক্স ===== | ===== - জিওমেট্রি থেকে ফিজিক্স ===== | ||
| নিশ্চিত প্রমাণের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আঠার শতক পর্যন্ত। কিন্তু এর মধ্যে নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়াই বেশির ভাগ এস্ট্রোনমার সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, | নিশ্চিত প্রমাণের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আঠার শতক পর্যন্ত। কিন্তু এর মধ্যে নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়াই বেশির ভাগ এস্ট্রোনমার সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, | ||
| + | |||
| + | প্রত্যেক এস্ট্রোনমারের মধ্যে একজন কসমোলজিস্ট বাস করে। ব্রাহিও কসমোলজিকেল মডেল বানিয়েছিল একটা যার কেন্দ্রে পৃথিবী, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | দ্বিতীয় সূত্র বলে, একটা গ্রহ তার এলিপ্টিকেল অর্বিটের কেন্দ্রে সমান সময়ে ($t$) সমান এরিয়া ($A$) সাবটেন্ড করবে। দূরে গেলে এরিয়া সরু হবে, কাছে আসলে এরিয়া চওড়া হবে, কিন্তু এরিয়ার মান পাল্টাবে না, যদি এরিয়ার আর্কটা পার হতে গ্রহের সমান সময় লাগে। উপরের এনিমেশনে বেগুনি এরিয়াটা সব সময় সমান। ক্যালকুলাসের ভাষায় | ||
| + | |||
| + | $$ \frac{dA}{dt} = \frac{J}{2m}$$ | ||
| + | |||
| + | যেখানে $J$ গ্রহটার এঙ্গুলার মোমেন্টাম, | ||
| + | |||
| + | $$ T^2 \propto r^3 \Rightarrow \left(\frac{r}{v}\right)^2 \propto r^3 \Rightarrow \frac{v^2}{r} \propto \frac{1}{r^2} \Rightarrow a_c \propto \frac{1}{r^2} $$ | ||
| + | |||
| + | যেখানে $v$ গ্রহের বেগ এবং $a_c$ তার সেন্ট্রিপেটাল এক্সিলারেশন, | ||
| + | |||
| + | $$ F_c = m a_c = GMm \frac{1}{r^2} $$ | ||
| + | |||
| + | যেখানে $G$ নিউটনের গ্র্যাভিটেশনাল কনস্টেন্ট, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | কোপার্নিকাস বৈপ্লবিক হলেও এরিস্টটলের দুইটা জিনিস ত্যাগ করতে পারেনি, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | এস্ট্রোনমিকে কসমোলজির মাধ্যমে গণিত থেকে ফিজিক্সে রূপান্তরিত করার কাজে এর পর অবশ্যই গ্যালিলিওর নাম বলতে হবে। ডাচদের দেখাদেখি টেলিস্কোপ বানিয়ে গ্যালিলিও ১৬১০ সালে প্রথম আকাশের দিকে তাক করে দেখেছিল অদেখা অনেক তারা, | ||
| + | |||
| + | নিউটন ১৬৮৭ সালে যখন [[wp> | ||
| + | |||
| + | ===== - রেভলুশনসের প্রমাণ ===== | ||
| + | ==== - এবারেশন: | ||
| + | বিশ শতকের আইনস্টাইন থেকে আমাদেরকে আবার আঠার ও উনিশ শতকে ফিরে যেতে হবে ' | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | [[aberration|আলোর এবারেশন]] হয় সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর বেগের পরিবর্তনের কারণে। উপরের ছবির মতো যদি ধরা হয় অনেক দূরের তারা থেকে আলো লম্বালম্বিভাবে পৃথিবীতে আমাদের উপর পড়ছে, | ||
| + | |||
| + | $$ \alpha = \theta-\phi = \frac{v}{c} $$ | ||
| + | |||
| + | যেখানে $\alpha$ এবারেশন, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | আঠার শতকের সবচেয়ে বড় এস্ট্রোনমারদের একজন ইংল্যান্ডের জেমস ব্র্যাডলি পৃথিবীর বেগের কারণে তারার পজিশনের এই পরিবর্তন পাব্লিশ করেছিল ১৭২৭ সালে। গামা ড্রাকোনিস (নীল কার্ভ) ও ৩৫ ক্যামেলোপার্ডালিস (লাল কার্ভ), | ||
| + | |||
| + | ==== - প্যারালাক্স: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | তবে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, | ||
| + | |||
| + | জ্যামিতিক হিসাব থেকে ব্র্যাডলি জানত যে প্যারালাক্সের কারণে গামা ড্রাকোনিস ডিসেম্বর মাসে তার বার্ষিক পথের সবচেয়ে দক্ষিণে থাকার কথা, এবং তারপর এক মাসের মধ্যে তার পজিশন খুব একটা পাল্টানোর কথা না। কিন্তু মাপতে গিয়ে সে দেখেছিল, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | এবং এবারেশনের ম্যাক্সিমাম কেন প্যারালাক্সের ম্যাক্সিমামের চেয়ে তিন মাস আগে-পরে হবে তাও সে বুঝতে পেরেছিল। প্যারালাক্স পৃথিবীর পজিশনের উপর নির্ভর করে, আর পজিশন হচ্ছে পৃথিবীর অর্বিটের রেডিয়াসের শেষ প্রান্ত, | ||
| + | |||
| + | ব্র্যাডলির কোনো অব্জার্ভেশনে যেহেতু প্যারালাক্স ধরা পড়েনি সেহেতু প্যারালাক্স নিশ্চয়ই ১ আর্কসেকেন্ডের কম। এবং আসলেই তাই। পাশের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, | ||
| + | |||
| + | $$ \tan p \approx p = \frac{a}{r} $$ | ||
| + | |||
| + | যেখানে $a$ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব, | ||
| + | |||
| + | জার্মানিতেই ফ্রিডরিখ বেসেল ১৮৩৪ সালে ৬১ সিগ্নি তারার প্যারালাক্স মাপার চেষ্টা শুরু করেছিল। স্ট্রুভের দাবিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বেসেল আরো নিবিড় পর্যবেক্ষণ শুরু করে এবং ১৮৩৮ সালে ৬১ সিগ্নি' | ||
bn/un/almagest-revolutions.1740816221.txt.gz · Last modified: 2025/03/01 01:03 by asad